শিক্ষায় অতিকচলানি কাম্য নয়

ছবি: ফাইল ফটো
মৌলিকতা বাদ দিয়ে শিক্ষা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে বেশি পর্যায়ে। সৃজনশীল, এমসিকিউসহ কতো কী? এমনিতেই দেশে অন্তত এগারো কিছিমের শিক্ষা ব্যবস্থা ধাবমান-চলমান। আবার মাঝেমধ্যে একমুখীতার কথা বলে বহুমুখীতার প্রবণতা। আজ বৃত্তি, কাল বৃত্তি তুলে দেয়া। যখন যেটা মন চায়, সেটার পক্ষে ব্যাপক যুক্তি। আর কিছু লোকের এতে সায় দিয়ে নেমে পড়া। বাহ, বাহ আওয়াজ আর কতো?
বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলোর বেশিরভাগই বেসরকারি বা এমপিওভুক্ত বেসরকারি। ছাত্রবেতন দিয়ে চলতে হয় শিক্ষা এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে। কখনো সরকারি, কখনো স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের কতো খবরদারি সইতে হয়, তা মর্মে মর্মে জানেন এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টরা। কিছুদিন তা চলেছে শিক্ষাবৃত্তি নিয়েও।
নতুন কারিকুলাম চালু হওয়ায় প্রাথমিক ও জুনিয়ার বৃত্তি উঠে গেছে। কারিকুলাম ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সাথে বৈপরীত্যের কারণ দেখিয়ে এটা বাতিল করা হয়েছে। আশির দশকের শুরুতে প্রাথমিক স্তরের শেষ ক্লাস ৫ম শ্রেণিতে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তির পরিমাণ ছিল মাসিক ৩০ টাকা এবং টেলেণ্টপুলে ১২৫ টাকা। অর্থাৎ সাধারণ গ্রেডের চেয়ে টেলেণ্টপুলে বৃত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪ গুণেরও বেশি। তখন জুনিয়র স্তরে মানে ৮ম শ্রেণিতে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তির পরিমাণ ছিল মাসিক ৫০ টাকা। টেলেণ্টপুলে ৩০০ টাকা, অর্থাৎ সাধারণ গ্রেডের চেয়ে ৬ গুণ বেশী। তখন মাধ্যমিক স্তরে স্কুলের বেতন ছিল শ্রেণিভেদে ৫ থেকে ২০ টাকার মধ্যে। অর্থাৎ বেতনের তুলনায় বৃত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫-১০ গুণ বেশি। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন ও ভর্তিবাবদ ব্যয় মওকুফ করা হতো বলে বৃত্তির টাকা দিয়ে তারা খাতা-কলম, বইপুস্তক, প্রাইভেট-কোচিং ইত্যাদি ব্যয় মেটাতে পারতো। নইলে কেউ কেউ সেখান থেকে কিছু সঞ্চয় করতো।
যে কারণেই হোক সরকার দীর্ঘদিন ধরে বেপরোয়াভাবে ছাত্রভর্তি ও পাশের হার বাড়িয়েছে। নানা কোটাও চালু করেছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়িয়েছে। এতে অনেক খরচের দাবি করা হয়েছে সরকারি তরফে। আসলে খরচটা কি খুব বেশি ছিল? করোনার আগে ২০১৯ সালে সরকার প্রাথমিক স্তরে টেলেণ্টপুলে বৃত্তি দিয়েছে ৩৩ হাজার শিক্ষার্থীকে। আর সাধারণ গ্রেডে ৪৯ হাজার ৫’শ জনকে। এতে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে টেলেণ্টপুলে খরচ হয়েছে ৯৯ লআখ টাকা। সেই হিসাবে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণি মিলিয়ে টেলেণ্টপুলে বছরে খরচ ২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। সাধারণ গ্রেডে বছরে খরচ ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ১২ হাজার ৫ শো টাকা। অন্যদিকে, ২০১৯ সালে জুনিয়র স্তরে টেলেণ্টপুলে বৃত্তি দেয়া হয়েছে ১৪ হাজার ৭০০ জনকে। সাধারণ গ্রেডে ৩১ হাজার ৫০০ জনকে। এতে জুনিয়র স্তরে (৯ম-১০ম শ্রেণিতে) বৃত্তি বছরে ৩ কোটি ২১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।
হিসাব একদম পরিস্কার। এ হিসাবে ২০১৯ সালে প্রাথমিক ও জুনিয়র মিলিয়ে সারা দেশের সাধারণ অভিভাবকের প্রায় দেড় কোটি সন্তানের মেধা-বৃত্তিতে সরকারের ৯ কোটি ৫২ লক্ষ ৪২ হাজার ৫ শো টাকা খরচ কি অনেক টাকা? ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের কোনো কোনো মাঠ নেতার বছরে আয়-ব্যয়ের হিসাবও এর চেয়ে বেশি। শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়আসয়ের একটা আলাপও এখানে হয়ে যেতে পারে। মাধ্যমিক স্তরে ধারাবাহিকভাবে নতুন বিজ্ঞান বই চালু করা হয়েছিল ১৯৮১ সাল থেকে। সেখানেও কমানোর প্রকল্প। ধরা যাক, ১৯৮১ সাল থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণির সাধারণ বিজ্ঞানের কথা। বইটির ১ম অধ্যায়-পরিমাপ। মোট বরাদ্দ ১৪ পৃষ্ঠা, অনুশীলনী ৩ পৃষ্ঠা। টেক্সট আলোচনা ১১ পৃষ্ঠা। ১১ পৃষ্ঠার টেক্সটে ল্যাবে বা হাতে-কলমে বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক করার কাজ ছিল ১৩টি, যার শিরোনাম ছিল ‘এসো নিজে করি’ এবং যার বর্ণনায় ব্যয় হয়েছে প্রায় ৮ পৃষ্ঠা। বাকি ৩ পৃষ্ঠা তত্ত, তথ্য ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।
ওইসব ‘নিজে করি’র কাজে ল্যাবে যেতে হবে বা ল্যাব উপকরণ খরচ বাস্তবে ছিল না। যে যেভাবে পেরেছে নিজে নিজে করেছে। পাস করেছে। পুরোটা এক ধরনের তামাশার মতোই।
শিক্ষা অন্য কটি খাতের মতো নয়, তা মনে না রাখলেও যেন কারো সমস্যা হচ্ছে না। যে কোনো কারিকুলাম প্রণয়ন, টেক্সট উপস্থাপন, অনুশীলন নির্ধারণ, মূল্যায়ন ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলো সবার আগে বিবেচনা করা হয়। পাঠ পরিকল্পনা ছিল প্রথমত প্রান্তের ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানে পিছিয়ে দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত হলো তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতি, কাঠামোগত সংস্কার, ইত্যাদির নামে ব্যাংক ও বাণিজ্যখাতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে লোকবল সরবরাহ বাড়াতে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কমিয়ে বাণিজ্যতে সরিয়ে নেওয়া, সে-কারণে এইসব প্রশ্ন একেবারেই বিবেচনা করার সুযোগ পরিকল্পনাকারীদের ছিল না, সরকার বা বিশেষজ্ঞদেরও ছিল না। আর যেহেতু বিজ্ঞান শাখা বন্ধ করে দিলে বা খোলার অনুমতি না দিলে সামাজিক প্রতিক্রিয়া হবে, শাখা খোলা ও ল্যাব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ব্যবসাও কম হবে, ফলে সেই নেতিবাচক পথ পরিহার করা ছিল খুবই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত। ফলে আশির দশকের শুরুতে এসএসসিতে বিজ্ঞান শাখার যতো শিক্ষার্থী ছিল, সব দিক বিবেচনা করে সেই সুন্দর বইটা দিয়ে নব্বই দশকের শুরুতেই তার প্রায় অর্ধেক কমানো সম্ভব হয় এবং পরিকল্পনা দারুণভাবে সফল হয়। এরপর আবার সেই বই ইভ্যালুয়েশন করে বাতিল করে ভিন্ন বিজ্ঞান বই প্রণয়ন করা হলেও বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা আর ফিরে আসেনি। ক্লাস নাইট-টেনে গণিত-বিজ্ঞান একটুও কমছে না বরং বাড়ছে—তবে গণিত-বিজ্ঞানের ভয়ে বা অপছন্দ থেকে যে ৩ ভাগের ২ ভাগ শিক্ষার্থী বাণিজ্য বা কলা শাখায় যেতো, তারা এখন কিভাবে উত্তীর্ণ হবে? নাকি ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ একটা মার্কা দিয়ে দিলেই হবে প্রশ্নফাঁস আর শতভাগ পাশের মতো করে? এ ধরনের অনেক প্রশ্ন থাকলেও জবাব নেই। জবাব দিতেও হয় না। এখনও হচ্ছে না। ভবিষ্যতে হয় কিনা , কে জানে!
লেখক:
সম্পাদক, বাংলাপোস্ট (সাপ্তাহিক)




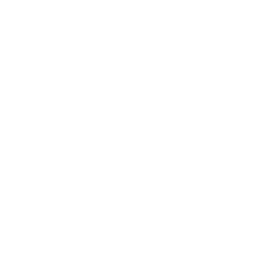
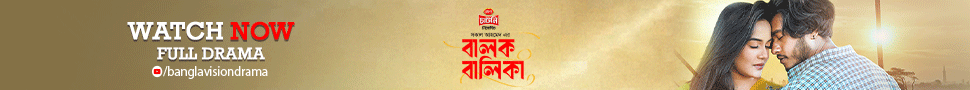














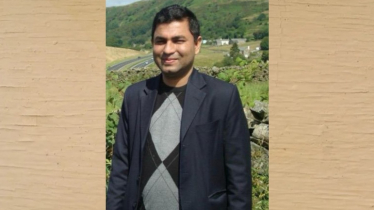


মন্তব্য করুন: