সাংবাদিকতা কি মত প্রকাশের প্ল্যাটফর্ম, না তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব? বিচারধারার সীমানা ও সংকট
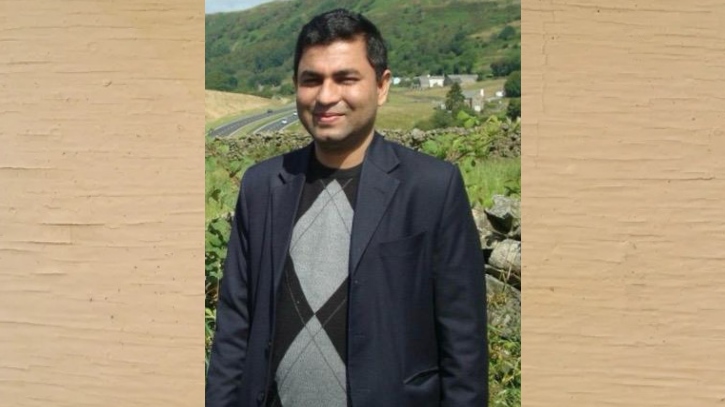
একজন রিপোর্টার প্রশ্ন করেন, কিন্তু মতামত দেন না। তিনি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের দায়িত্বে থাকেন, পক্ষ নেন না। এই মৌলিক নীতিটি পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলোতে বহু বছর আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত। অথচ আমাদের দেশে, এখনো রিপোর্টারদের মতামত প্রকাশের চর্চা চলছেই এবং কখনো কখনো তা অতি আবেগে পেশাদারিত্বের সীমা লঙ্ঘন করে।
সম্প্রতি উপদেষ্টা ফারুকীর এক সংবাদ সম্মেলনে দীপ্ত টিভির রিপোর্টার মিজানুর রহমানের আচরণ এই বিতর্কের কেন্দ্রে এসেছে। তিনি প্রশ্নের বদলে বললেন, ‘এটা তো যারা রাজনীতিবিদ তারা বলবে’ কিংবা ‘আপনি বায়াসড উত্তর দিলেন’। এই বক্তব্যগুলো মতামত না হয়ে কী? সংবাদ সম্মেলনে একজন রিপোর্টার নিজের কাভার করা বিষয়ে এভাবে প্রকাশ্যে মতামত দিলে তা রিপোর্টিংয়ের গণ্ডি পেরিয়ে যায়। হোয়াইট হাউজে হলে এ ধরনের আচরণ নিয়ে রিপোর্টারকে জবাবদিহি করতে হতো।
মতামত সাংবাদিকতা: পেশার এক স্বীকৃত ধারা
বিশ্বের বড় বড় গণমাধ্যম যেমন নিউ ইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, আল জাজিরা-এদের অনেকেই মতামতভিত্তিক সাংবাদিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। মেহেদী হাসান, অ্যান্ডারসন কুপার, কিংবা সিরিল আলমেইডা-তারা বিশ্লেষক ও মতামত সাংবাদিক। তারা রিপোর্ট করেন, কিন্তু তাদের অবস্থান স্পষ্ট এবং তার জন্য তাদের পাঠক প্রস্তুত। এটা এক ধরনের ভিন্ন সাংবাদিকতা।
বাংলাদেশের সাংবাদিকতার শিকড়ও এ ধারায়। মানিক মিয়া, মাহফুজ আনাম, এবিএম মূসার মতো সাংবাদিকেরা অধিকাংশ সময়ে মতামত সাংবাদিকতা করেছেন। কিন্তু তারা রিপোর্টার ছিলেন না, তারা বিশ্লেষক, সম্পাদক, দিকনির্দেশক। সুতরাং রিপোর্টার এবং কমেন্টেটরের মধ্যে বিভাজন থাকা উচিত।
পশ্চিমে বিভাজন স্পষ্ট, আমাদের দেশে ধোঁয়াশা
বিশ্বের অধিকাংশ সিরিয়াস নিউজরুমে রিপোর্টিং ও অপিনিয়ন একে অপর থেকে আলাদা। নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, গার্ডিয়ান, ব্লুমবার্গ—সবাই রিপোর্টারদের মতামত প্রকাশে নিষেধ করে। ব্লুমবার্গ তো মতামত বিভাগেই সাংবাদিক রাখতে চায় না। কারণ রিপোর্টারদের বিশ্বাসযোগ্যতা তথ্যনির্ভরতা ও নিরপেক্ষতার ওপর দাড়িয়ে থাকে। একবার মতামত দিলে সেই নিরপেক্ষতার মেরুদণ্ডে চিড় ধরে।
আমাদের দেশে সেই বিভেদ এখনো তৈরি হয়নি। একজন রিপোর্টার কলাম লিখছেন, টকশো করছেন, ফেসবুকে মতামত দিচ্ছেন এবং এসব করছেন একই সঙ্গে সরকারের বা বিরোধী দলের বিট কাভার করেও। এতে পাঠকের কাছে সেই রিপোর্টারের রিপোর্ট আর মতামতের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। ফলে রিপোর্টিং বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়, যা পুরো সাংবাদিকতা পেশাকেই আঘাত করে।
উপদেষ্টাদের সংবাদ সম্মেলন, প্রতিবাদ, এবং নীরবতা
এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- ইউনূস সরকারের অধীনে সাংবাদিকদের স্বাধীনতার বাস্তব চিত্রটি কেমন? একটি স্পষ্ট ঘটনা ঘটেছে, দুই রিপোর্টারকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে মত প্রকাশের প্রেক্ষিতে, যেটা আগের সরকারের সময় ঘটলে চরম প্রতিবাদ হতো। অথচ এখন ইউনূস সরকারের তথাকথিত ‘মুক্ত সাংবাদিকতার’ বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন করলেই কেউ কেউ অস্বস্তিতে পড়ছেন।
সরকারের তরফে বলা হয়েছে, তারা সংবাদ বন্ধ করেনি। পলক সাহেব বলেছেন, ইন্টারনেট বন্ধ করেননি। কিন্তু বাস্তবতা বলছে-নির্বাচনের সময় অনলাইন নিউজপোর্টালগুলো ব্লক হয়েছিল, সংবাদবহুল ইউটিউব চ্যানেলগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল। এই বাস্তবতা নিয়ে কোনো স্বাধীন সাংবাদিক সম্মেলন হয়নি। ইউনূস সরকারের পক্ষ থেকে কেউ আসেননি এসব ব্যাখ্যা দিতে।
আমরা যারা সাংবাদিকতার স্বাধীনতা চাই, তাদের উচিত এইসব প্রশ্ন উত্থাপন করা। অবশ্যই পেশাদারিত্ব বজায় রেখে। মতামত সাংবাদিকতা করতে চাইলে সেটার জন্য আলাদা জায়গা আছে। কিন্তু রিপোর্টার হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে গিয়ে মতামত দিতে চাইলে সেটা সাংবাদিকতার নীতিগত চ্যুতি।
প্রেসক্লাব কি সাংবাদিকদের?
আরেকটি ভুল ধারণা হলো প্রেসক্লাব নিয়ে। প্রেসক্লাব আসলে সাংবাদিকদের জন্য কোনো বিশেষায়িত নীতিগত প্রতিষ্ঠান নয়। এটি একটি ক্লাব মাত্র, যেটার কার্যক্রম অনেকটাই সামাজিক ও পেশাগত যোগাযোগ কেন্দ্রিক। কিন্তু এই ক্লাব নিয়েই সাংবাদিকদের একাংশ যখন অভিমান বা ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তখন বোঝা যায় পেশার মৌলিক বিষয়গুলো এখনো ঠিকমতো আত্মস্থ হয়নি।
শেষ কথা
সাংবাদিকতা শুধু মতপ্রকাশ নয়। এটা তথ্য পরিবেশনের কঠিন, দায়িত্বপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক চর্চা। একজন রিপোর্টার তথ্য উপস্থাপন করেন, পক্ষ নেন না। পক্ষ নিতে হলে তার পরিচয় পাল্টাতে হবে। তাকে হতে হবে মতামত সাংবাদিক, কিংবা রাজনৈতিক ভাষ্যকার। এই স্পষ্ট সীমারেখা মেনে চলা না গেলে আমাদের মিডিয়া আর পেশাদার থাকবে না, হয়ে পড়বে কেবল মতান্ধতার প্রতিচ্ছবি।
লেখক: ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম রেজাউল করিম
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী গবেষণা কেন্দ্র
বিভি/এসজি




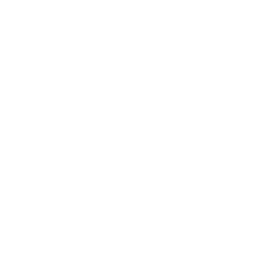
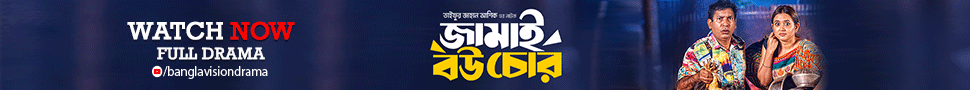














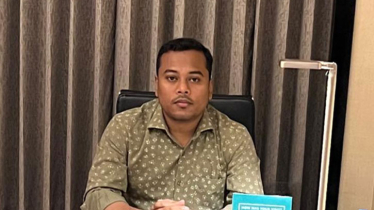


মন্তব্য করুন: