কূটনীতিকদের `কফি গ্রুপ`, সুযোগ করে দিচ্ছেন রাজনীতিকরাই

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত বিরোধিতা একসময় খুব শোনা যেত। ‘শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে ভারতকে অনুরোধ করেছি’- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এমন একটি বক্তব্য দেয়ার পর এটি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে তুমুল আলোচনা হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন গণতন্ত্র শক্তিশালী ভিত না পাওয়ার কারণেই বাংলাদেশে প্রায়ই বিদেশী শক্তিগুলো প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে পঁচাত্তরের পটপরিবর্তন, পরবর্তীতে একাধিক সামরিক শাসন, ১৯৯০ সালে জেনারেল এরশাদের পতন, এমনকি ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর প্রতিটি রাজনৈতিক সঙ্কট এবং কমবেশি সব নির্বাচন ঘিরে প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে বিদেশীদের তৎপরতা আলোচনায় এসেছে।
বাংলাদেশসহ ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল এমন বেশির ভাগ দেশেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্ত হতে পারেনি বলেই বিদেশী শক্তিগুলো প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। এসব দেশের তুলনামূলক দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থাও একটি বড় কারণ যার সুযোগ প্রভাবশালী দেশ বা গোষ্ঠীগুলো নিয়ে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র না থাকা আর দেশটির ভূরাজনৈতিক অবস্থানের কারণে বিদেশীদের প্রভাব এড়ানো যায় না।
স্লোগানে, নীতিতে বিদেশীদের প্রভাব :
বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘকাল দু’টি স্লোগান ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। একটি হলো ‘রুশ ভারতের দালালরা-হুঁশিয়ার সাবধান’ আর অন্যটি হলো ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-নিপাত যাক, নিপাত যাক’। অর্থাৎ এখানে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে হয় রাশিয়া ও ভারতের না হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষাকারী এজেন্ট বা দালাল হিসেবে প্রকাশ্যেই চিত্রিত করত। বাংলাদেশ আমলে মূলত এটি শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ থেকেই যখন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আর রাশিয়া ও ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। ‘মূলত মুক্তিযুদ্ধের পরে সরকার রাশিয়া ভারতের একচ্ছত্র সমর্থন পেয়েছিল। বিরোধীরা সেটাকেই স্লোগানে পরিণত করেছিল। এরপর আওয়ামী লীগকে দীর্ঘকাল ধরে তার বিরোধীরা ভারত ঘনিষ্ঠ হিসেবে প্রচার করেছে’।
১৯৭৫ সালের পর পুরো দৃশ্যপট বদলে যায় এবং সামনে চলে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এরপর দীর্ঘকাল সামরিক শাসনে বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্লোগানে উত্তপ্ত ছিল রাজপথ। এসব কারণে জনমনেও বিভিন্ন দলের বিদেশী শক্তিপ্রীতির দিকগুলো নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। বামপন্থী কিছু রাজনৈতিক দল তো চীন বা রাশিয়াপন্থী হিসেবে প্রকাশ্যেই পরিচিত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রও ধীরে ধীরে তার কৌশলে পরিবর্তন আনে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। একপর্যায়ে ভারত হয়ে পড়ে এ অঞ্চলের প্রভাবশালী রাষ্ট্র। আর ভারতের প্রভাব ঠেকাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে চীন।
ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ভারত আর চীন হয়ে ওঠে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে এখন যে সরকার আছে তাতে ভারতের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে তখনকার ভারতীয় কর্মকর্তা সুজাতা সিংয়ের তৎপরতায়ও কোনো রাখঢাক ছিল না । অন্য দিকে বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তারা ‘লুক ইস্ট পলিসি’ নিয়েছিল। সেখানে চীনের প্রতি তাদের আস্থা বেশি প্রকাশ পেয়েছিল। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মোটামুটি ভারসাম্য রক্ষা করে আসছিল। অর্থনৈতিক অবস্থা যখন একটু একটু ভালো হচ্ছিল তখন অনেক সময় ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রকে শক্ত কথাও বলতে দেখা গেছে মাঝে মধ্যে। আসলে অর্থনীতি ভালো হলে তখন আর কারো দ্বারস্থ হওয়ার দরকার হয় না।
“সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবশালী দেশগুলো সবসময় সক্রিয় থাকে। তারা চায় অন্য দেশের সরকারগুলো তাদের ঘনিষ্ঠ হোক। আবার দেশের অভ্যন্তরে যারা রাজনীতি করে তারা চিন্তা করে ‘বড় ভাই’দের কাছে না গেলে আমার কোন পরিণতি হয় কে জানে। এসব কারণেই দেশের রাজনীতিতে বিদেশীদের প্রভাব বাড়তে থাকে।” ‘বাংলাদেশে এখন যে সরকার আছে সেটি ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট’ এবং এটি যারা সমর্থন করে তারাই ভারতপন্থী আর যারা বিরোধিতা করে তারা ভারতবিরোধী। আর যারা ভারতবিরোধী তাদের কেউ কেউ আবার রাজনৈতিক অঙ্গনে পাকিস্তানপন্থী হিসেবে পরিচিত।
নতুন বৈশ্বিক বাস্তবতায় বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের প্রবল আগ্রহ এখন বাস্তবতা। বিশ্লেষকরা অনেকে মনে করেন আগে আওয়ামী লীগকে ভারতের সমর্থনপুষ্ট হিসেবে তার প্রতিপক্ষ বিএনপি নেতারা প্রচার করলেও ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর বিএনপিও নানাভাবে চেষ্টা করেছে ভারতের সমর্থন আদায়ের। দলটির সাবেক মহাসচিব মরহুম খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন কাউকে ‘ব্লাইন্ড সাপোর্ট’ না দেয়ার প্রকাশ্যে ভারতকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, যা ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। এর আগে ও পরে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনে বিদেশীদের মধ্যস্থতা করা কিংবা সিভিল সোসাইটিগুলোর মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা এমন অনেক কিছুই আলোচনায় এসেছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে।
‘ধরুন একটি সামরিক প্রভাবশালী রাষ্ট্রের কথা শোনা হলো না, তখন সে হয়তো অর্থনীতিতে বাধা তৈরি হয় এমন পদক্ষেপ নেবে। কিংবা অন্য কোনো উপায়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করতে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করবে।’ ‘আবার কেউ হয়তো হুট করে বাংলাদেশের জন্য জরুরি কোনো পণ্য বাংলাদেশে রফতানি বন্ধ করে দেবে, যাতে সরকার বিপাকে পড়ে যায়। এ কারণে একটি ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। আবার একই কারণে রাজনৈতিক দলগুলোরও চেষ্টা থাকে প্রভাবশালীদের সন্তুষ্ট রাখতে।’‘আবার সমর্থন না করে চুপ থাকলেও হবে না। কারণ বড় ভাইয়ের কাছে না গেলে সেটি তারা ভালোভাবে নাও নিতে পারেন।
এ কারণেই বৈশ্বিক রাজনীতিতে অ্যাকটিভ প্লেয়ারদের নিয়ন্ত্রণ এড়ানো কঠিন হয় অনেক সময়।’ এখন বিদেশী প্রভাব ইস্যুতে রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যমও সিভিল সোসাইটিসহ সবার মধ্যে আরো পরিপক্বতা আসা দরকার। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশী কয়েকজন ব্যক্তির ওপর মর্কিন নিষেধাজ্ঞাকেও আগামী নির্বাচন সামনে রেখে চাপ তৈরির কৌশল বলে বর্ণনা করেন অনেক বিশ্লেষক। যদিও এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হয়ে গণতন্ত্র কার্যকর না হলে সেটিও হওয়া কঠিন বলে মনে হয় ।
সে কারণে আরো কিছুকাল প্রভাবশালী দেশগুলোর সমর্থন আদায় নিয়ে প্রতিযোগিতাও বড় দলগুলোর মধ্যে চলতে থাকবে বলে তার ধারণা। বিগত সময়ে দেশের রাজনীতিতে ঢাকায় কূটনীতিকদের 'কফি গ্রুপ' ছিল খুব আলোচিত। দুই হাজার ছয় সালের শেষ দিকে এবং ২০০৭ সালের প্রথম দিকে ঢাকায় নিযুক্ত পশ্চিমা দেশের কিছু কূটনৈতিক ছিলেন বেশ তৎপর। এদের মধ্যে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রেসিয়া বিউটেনিস, ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী এবং ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি রেনাটা লক ডেসালিয়ান ছিলেন সবচেয়ে বেশি সক্রিয়।
রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য তারা দফায়-দফায় খালেদা জিয়া এবং হাসিনার সাথে বারবার বৈঠক করেছেন। উইকিলিকসে প্রকাশিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্যাট্রেসিয়া বিউটেনিসের গোপন তারবার্তা থেকে জানা যায়,ঢাকাস্থ পশ্চিমা কূটনীতিকরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য নিজেদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক করতেন। যার নাম দেয়া হয়েছিল 'কফি গ্রুপ'। এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি এবং জাতিসংঘের প্রতিনিধি। এই গ্রুপে জাপানকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।
সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে নানা আয়োজন করেন ঢাকাস্থ পশ্চিমা কূটনীতিকরা। বাংলাদেশের সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে তারা প্রায়ই বিবৃতি দিতেন। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক যাতে একই ধরণের উদ্বেগ প্রকাশ করে সেজন্য পদক্ষেপ নিতে ঢাকাস্থ কূটনীতিকরা লন্ডন এবং ওয়াশিংটনকে জানান। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের গোপন তারবার্তা থেকে জানা যায়, সৌদি আরবের পররাষ্ট্র দফতর কিংবা ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাস যাতে পশ্চিমাদের মতো উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি দেয় সেজন্য পদক্ষেপ নিতে ওয়াশিংটনকে পরামর্শ দেয়া হয়।
বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এলে বিদেশি কূটনীতিকদের কথাবার্তা বেড়ে যাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। আগের বেশ কয়েকটি নির্বাচনেও এমনটি দেখা গিয়েছিল। এটি সত্যি যে আমাদের গণতন্ত্রে এখনো কিছু ঘাটতি রয়ে গিয়েছে। আর দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বৈরী সম্পর্ক এ ধরনের কথা বলার সুযোগ তৈরি করে দেয়। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কখনো এমন কোনো সিদ্ধান্তেও পৌঁছাতে পারেনি, যা বিদেশিদের কথা বলার পথ বন্ধ করে দিতে পারে। আবার বিরোধী দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের সংস্কৃতি চালু রয়েছে যে বিদেশিরা সরকারি দলের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কথা বলুক। সরকারি দলগুলো অবশ্য এ বিষয়টি তেমন পছন্দ করে না। এটি বাংলাদেশের রাজনীতির একটি নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।
বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে অনেক ক'টি পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। প্রথম, রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হতে হবে । বিভিন্ন পর্যায়ে দলের নেতৃত্ব সুনির্দিষ্ট হতে হবে দলীয় নেতাকর্মীর রায়ে, নির্বাচনের মাধ্যমে। বর্তমানে তা হচ্ছে না। দলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে যারা রয়েছে তাদেরও নির্বাচনের মাধ্যমে আসতে হবে। দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে দলের নেতাকর্মীদের দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে যেন তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ শক্তিশালী হয় এবং জনগণের সাথে যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারে এবং দলের বিস্তৃতি ব্যাপক এবং গভীর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়, গণতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ করতে হলে দলীয় নেতাকর্মীর মন- মানসিকে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিক - সমৃদ্ধ হতে হবে। সহিষ্ণুতা এবং সমঝোতার মানসিকতা এক্ষেত্রে মণিকাঞ্চন স্বরূপ। উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজে নেতা হলেন একজন আপোষকামি, জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ধারণকারি, যোগাযোগ দক্ষ, অগ্রবর্তী ভাবনায় উদ্দীপ্ত, জনস্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে পূরোপুরি সচেতন কর্মকর্তা। বাংলাদেশে কিন্তু নেতা হলেন পরম পরাক্রমশালী দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, সব কিছুতে চুড়ান্ত রায় দানকারী, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, নির্জন প্রকোষ্ঠ বসবাসকারী, মহামহিম আদেশ দানকারী শ্রদ্ধেয় এক মহান কর্মকর্তা। এই অবস্থার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। তৃতীয়, গণতন্ত্র হলো নিয়মতান্ত্রিক সীমিত সরকার আর সংসদীয় গণতন্ত্র মূলত দ্বিদলীয় কাঠামোয় (Bi partisan) সংগঠিত সরকার । এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রযুক্ত হয় আইনি কাঠামোয়, ব্যক্তির নির্দেশে নয়, ব্যক্তির ইচ্ছা- অনিচ্ছায় তো নয়ই । চতুর্থ, আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। সাথে সাথে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্যে একরাশি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। পঞ্চমত, গণতন্ত্রের যেহেতু ব্যক্তিগত ক্ষমতা ( Personalized ) প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই, তাই রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগের জন্যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃত্বব্যঞ্জক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন সরকারি কর্মকর্তাদের মেধা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়োগদান, দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে নয়। ষষ্ঠ, গণতন্ত্র একটি পরিপূর্ণ প্রত্যয়, আংশিক কোনো প্রত্যয় নয়। তাই গণতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ করতে হলে চলবে না । সমগ্র সমাজব্যাপী, কেন্দ্র ও প্রান্ত মিলিয়ে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটাতে হবে। অন্যকথায়, কেন্দ্রে তো বটেই, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকেও গণতান্ত্রিক এবং শক্তিশালী করতে হবে ।
এখন আমাদের দেশে পশ্চিমা কাঠামোর আদলে গণতন্ত্র পুনরুৎপাদন করব, সেই চিন্তাটি পর্যালোচনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমা দেশগুলো তাদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে উপনিবেশিক লুণ্ঠনের মাধ্যমে। তারা উপনিবেশিক লুণ্ঠন আর এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দাসপ্রথা দিয়ে সম্পদের পাহাড় তৈরি করেছে। বাংলাদেশ তো আর উপনিবেশিক লুণ্ঠনে জড়িত হয়নি। সামনে সে সুযোগও নেই। তাই আমাদের আদলে কীভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেটি নিয়ে ভাবতে হবে। আমি প্রায়ই শুনি, গণতন্ত্র নিয়ে আর কিছু করার নেই। এখানকার গণতন্ত্র নিয়ে কাজ করার সুযোগ শেষ হয়ে গিয়েছে। আমার মতে, এ ধরনের হতাশায় না থেকে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কী ধরনের গণতন্ত্র চায়, সেটি বোঝা দরকার। অধিকাংশ মানুষ খাদ্য, বস্ত্র আর বাসস্থানের নিশ্চয়তা চেয়ে যে গণতন্ত্র চায়, সেই ভাবনাটিকে গুরুত্ব দিতে হবে । আমার মনে হয়, আমরা যে গণতন্ত্রের কাঠামো এখানে তৈরি করেছি, তার সঙ্গে জনগণের আকাঙ্ক্ষার একটি দূরত্ব রয়েই যাচ্ছে । আর একারণে গণতন্ত্রে ঘাটতি ও থেকে যাচ্ছে । সুতরাং সেদিকে বড় ধরনের মনোযোগ দেয়া দরকার বলে আমি মনে করি ।
লেখক: ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বাংলা পোস্ট
(বাংলাভিশনের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, বাংলাভিশন কর্তৃপক্ষের নয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো প্রকার দায়ভার বাংলাভিশন নিবে না।)




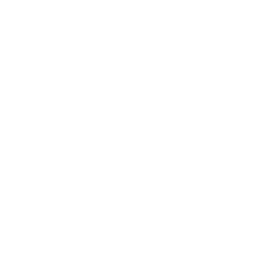
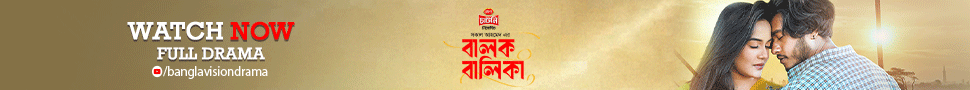














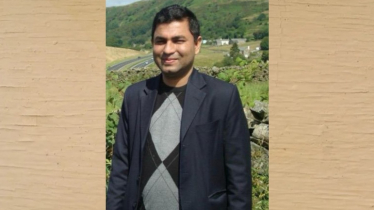


মন্তব্য করুন: