১৮৫ বছরে পদার্পণ: ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোয় আলোকিত ঢাকা কলেজ

উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কলেজ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪১ সালের ২০ নভেম্বর। গ্ৰিক দার্শনিক সক্রেটিসের ঐতিহাসিক বাণী 'Know Thyself' অর্থাৎ নিজেকে জানো প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখেই শুরু হয় পাশ্চাত্যের দর্শন,বিজ্ঞান এবং কলাবিদ্যা চর্চা। প্রতিষ্ঠানটিতে শুধু দেশের নয় বিদেশ থেকেও পড়তে আসতেন এক ঝাঁক মেধাবী শিক্ষার্থী। যার হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক এবং দেশবরেণ্য অনেক রাজনীতিবিদের পথচলা এই প্রতিষ্ঠান থেকে। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, ৯০র স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং সর্বশেষ ছাত্র জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থানসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা কলেজের অবদান অনস্বীকার্য। নানাবিধ চড়াই- উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে আজ (২০ নভেম্বর) ১৮৫ তম বছরে পদার্পণ করলো ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজ।
১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী ৬২ বছর পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকেরা পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য কোনো শিক্ষানীতি প্রনয়ণ বা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এ দীর্ঘ সময়ে এ অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থা ঐতিহ্যগতভাবেই চলছিলো। অবশেষে ১৮৩০-এর দশকে সরকার পাশ্চাত্য বা ইংরেজি শিক্ষানীতি গ্রহণ করে।
এ আধুনিক ধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সেসময়ে ঢাকাতে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৮৩৫ সালের ২০ এপ্রিল জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন লর্ড বেন্টিককে জানায় যে সরকারের তত্ত্বাবধানে বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রধান শহরগুলোতে ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যত বেশি সম্ভব বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। এ প্রস্তাবের পর ঢাকার সিভিল সার্জন ডা. জেমস টেইলার জানান, এখানে বিদ্যালয় স্থাপনের সব সুবিধা রয়েছে। মূলত তখন থেকেই শুরু হওয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৮৩৫ সালের ১৫ জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছিলো ঢাকা ইংলিশ সেমিনারী যা বর্তমানে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত।
এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যেমন সমাজের সামগ্রিক চিত্রে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে, তেমনি শিক্ষার্থীদের মানসজগতে উন্মোচিত হয় পাশ্চাত্যের কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান ও দর্শনের নতুন দিগন্ত। শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থার এ ইতিবাচক রূপান্তরকে আরও সুদৃঢ় করতে সে সময়ের গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড এবং জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কয়েকটি কেন্দ্রীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।
এর ধারাবাহিকতায় প্রস্তাবিত ব্যয় উল্লেখ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের পর ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর ঢাকা ইংলিশ সেমিনারী স্কুলকে একটি কলেজ বা আঞ্চলিক উচ্চতর ইংরেজি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হয়। নতুন প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজ, পরবর্তীতে যা ঢাকা কলেজ নামে পরিচিতি পায়। আর ঢাকা ইংলিশ সেমিনারী স্কুলের নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল।
এ কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই ঢাকার সামগ্রিক চিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ঢাকা ধীরে ধীরে পরিণত হয় সমগ্র পূর্ববাংলার ইংরেজি শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে।
১৮৪১ সালে ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠার পর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং হিন্দু কলেজের শিক্ষক জে. আয়ারল্যান্ডকে ঢাকা কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা হয়। তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে থাকে ঢাকা কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার ভিত্তি।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরপরই ঢাকা কলেজকে এর অধিভুক্ত করা হয়। সে সময় থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থরা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হলেও এর কাঠামোগত পরিবর্তনে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
১৮৫৯-৬০ সালের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে ঢাকা কলেজে যে পাঠ্যক্রম চালু ছিল, তা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষার সমমানের। কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পাঁচটি প্রধান শাখায় পরীক্ষা দিতে হতো। এসব বিষয় ছিল, ইংরেজিসহ দুটি ভাষা,ইতিহাস ও ভূগোল, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা) এবং মানসিক ও নৈতিক বিজ্ঞান। এসব বিষয়ে পাঠদানের মান ছিল অত্যন্ত উচ্চ, এবং শিক্ষার্থীদের সেই উচ্চ মান অর্জন করাই ছিল মূল লক্ষ্য।
১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি একটি বড় সম্মান অর্জন করে। এর মাধ্যমে পূর্ববাংলার তরুণরা প্রথমবারের মতো আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ লাভ করে এবং কলেজের অবকাঠামোতেও উন্নয়ন ঘটে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা কলেজের দীর্ঘ ঐতিহ্য ও গৌরবের পেছনে বহু মনীষীর অবদান রয়েছে। বাংলার সুপরিচিত ঐতিহাসিক গান ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ গানের রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরী ছিলেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী। এখান থেকেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল হুমায়ূন আহমেদ ও হুমায়ূন আজাদ। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিখ্যাত উপন্যাস ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর লেখক, বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক আক্তারুজ্জামান ইলিয়াসও এই প্রতিষ্ঠানের কৃতী শিক্ষার্থী ও শিক্ষক ছিলেন।
ঢাকা কলেজের আরেক গৌরব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭তম উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, যিনি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।
এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হিসেবে যুক্ত ছিলেন দেশের বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান এবং আ. ক. ম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, এ সকল প্রভাবশালী রাষ্ট্রনায়ক এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
শিক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও জাতীয় আন্দোলনে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা অগ্রণী ভূমিকা রেখে এসেছে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ’৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ’৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থান,সবসময়ই তারা জীবন বাজি রেখে নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন।
১৯৫২ সালের মহিমান্বিত ভাষা আন্দোলনে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী প্রথম সারির দলগুলোর অন্যতম নেতৃত্ব দেয়। তাদের সাহসী ভূমিকা ও আত্মত্যাগ ভাষা শহীদদের ত্যাগকে আরও গৌরবান্বিত করে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা কলেজ তার ৮ জন বীর শিক্ষার্থীকে শহীদ হিসেবে হারায়। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের এই সর্বোচ্চ ত্যাগ জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।
এ ছাড়া ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানসহ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ গণআন্দোলনে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং সর্বশেষ ২৪শের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তাদের অবদান ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অনস্বীকার্য।
দেশের সবচেয়ে প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে চারটি ভবনে শ্রেণি উপযোগী কক্ষ রয়েছে ৫২টি। শিক্ষার্থীদের আবাসনের জন্য ৮টি ছাত্রাবাস রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের ১৯টি বিভাগ মিলিয়ে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী পাঠদান করছে।
বিভি/এসজি




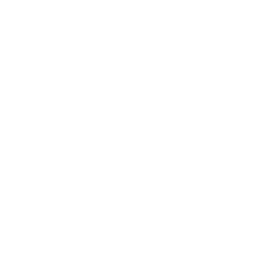

















মন্তব্য করুন: