আকাশমণি ও ইউক্যালিপ্টাস কি সত্যিই খারাপ গাছ?

ইনসেটে ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, এই নিবন্ধের লেখক।
জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে বিশ্বব্যাপী অনেক পরিবেশবাদী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদমাধ্যম এখন সোচ্চার। যে কোনো দেশেই উন্নয়ন ধারার প্রথাগত পদ্ধতিতে সামান্য বিচ্যুতিতেই তাঁরা সরব হয়ে ওঠেন। এই হৈ চৈ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে হবে না। কারণ, এটি সাধারণ মানুষকে সচেতন করে। বিজ্ঞানীদের সামনে তুলে ধরে পরিবেশ বিষয়ক গবেষণার নানান ইস্যু। বিজ্ঞানীরা গবেষণা শেষে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করেন; যা প্রকাশিত হয় দেশীয় বা আন্তর্জাতিক জার্নালে। তবে সংবাদমাধ্যম বা পরিবেশবাদীরা সব সময় বৈজ্ঞানিক তথ্য যথাযথভাবে পান না বলেই বিজ্ঞান এবং আবেগের মধ্যে দূরত্ব থেকে যায়। সংবাদ মাধ্যমগুলোর কাছে সঠিক তথ্য দিতে পারলে তারা সরকারের বিভিন্ন মহলে তা উপস্থাপন করতে পারে। এতে নীতিমালা তৈরিতে সরকারের সুবিধা হয়। অল্প সময়ে সেই তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেও যায়।
আমরা যারা বন সংরক্ষণ বা বন ব্যবস্থাপনায় কাজ করি, তাঁদের বিরুদ্ধে মিডিয়া এবং পরিবেশবাদীদের অভিযোগের শেষ নেই। সব অভিযোগ যে অমূলক তা-ও বলছি না। তবে বেশিরভাগ সময়ই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সীমাবদ্ধতার কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকে না। অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও আমরা যা অর্জন করছি, তা অনেক সময় তুলে ধরা হয় না। যেমন- বন বিভাগের বা বন গবেষণার সাফল্যের কাহিনী দেশের মানুষ জানেন না। অথচ উপকূলীয় বনায়নে বিশ্বের কাছে এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশ। ১৯৬০ সালের পরে প্রায় ২০০,০০০ হেক্টর উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন বনজ সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি উপকূলীয় এলাকার মানুষ ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ধ্বংস থেকে অনেকাংশে রক্ষা পেয়েছেন। রক্ষা পেয়েছে তাঁদের সম্পদ। উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের ফলে সেখানকার মাটি চাষোপযোগী হয়েছে। ভূমির ক্ষয়-রোধ হওয়ায় ভূমির পরিমাণও বাড়ছে।
উপকূলীয় বনায়নে কেন তাল বা সুপারি লাগানো হয়নি, তা নিয়ে বন বিভাগ বা বন সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে পরিবেশবাদীদের সমালোচনা সইতে হয়। তাল, নারিকেল বা সুপারি উপকূলীয় অঞ্চলে অবশ্যই লাগানো যায়। এগুলোর শিকড় মাটি আঁকড়ে ধরে। ঝড়-তুফানে সহজে উপড়ে পড়ে না। কিন্তু অনেক পরিবেশবাদীরই হয়তো জানা নেই, এসব গাছও বিদেশি।
আমাদের জমি সীমিত। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১০০’র বেশি মানুষ বাস করেন। সেই মানুষের চাহিদা বিবেচনায় দেশি গাছের পাশাপাশি বিদেশি দ্রুত বর্ধনশীল গাছের পরীক্ষামূলক বনায়ন শুরু হয় ষাটের দশকে। এর আগে ব্যক্তি উদ্যোগে অনেক বিদেশি গাছ চা-বাগানসহ বিশেষ বিশেষ স্থানে আনা হয়।
বিদেশি গাছ মানেই খারাপ, এমন ধারণা অনেকের। অথচ আমরা অনেকেই জানি না, দেশীয় গাছ বলে পরিচিত অনেক গাছই কিন্তু বিদেশি। ফলদ গাছের ক্ষেত্রে এটি তুলনামূলকভাবে বেশি। যদিও সময়ের পরিক্রমায় এসব গাছ আমাদের হয়ে গেছে। যেমন- কাঁঠাল, এসেছে ভারতের ওয়েস্টার্নঘাট থেকে, বাবলা এসেছে আফ্রিকা থেকে, রেন্ডিকড়ই ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে, সফেদা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে, রাজকড়ই মাদাগাস্কার থেকে, সুপারি ফিলিপাইন থেকে, নারিকেল ইন্দোনেশিয়া থেকে এবং তাল সেন্ট্রাল আফ্রিকা থেকে।
উপকূলীয় বনায়নে কেন তাল বা সুপারি লাগানো হয়নি, তা নিয়ে বন বিভাগ বা বন সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে পরিবেশবাদীদের সমালোচনা সইতে হয়। তাল, নারিকেল বা সুপারি উপকূলীয় অঞ্চলে অবশ্যই লাগানো যায়। এগুলোর শিকড় মাটি আঁকড়ে ধরে। ঝড়-তুফানে সহজে উপড়ে পড়ে না। কিন্তু অনেক পরিবেশবাদীরই হয়তো জানা নেই, এসব গাছও বিদেশি। বিদেশ থেকে এসে আমাদের পরিবেশে মিশে গেছে, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করেছে। কাজেই বিদেশি গাছের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়।
উপকূলীয় বনায়ন ছাড়াও বিশ্বে আরেকটি কারণে সুপরিচিত বাংলাদেশ। তা হচ্ছে সড়ক বনায়ন। রাস্তার দু’ধারে এতো বেশি গাছ, খুব কম দেশেই দেখা যায়। বনবিভাগের সামাজিক বনায়ন এই সাফল্যের দাবিদার। তবু সামাজিক বনায়ন বা সড়ক বনায়ন নিয়ে সমালোচনার কমতি নেই। সামাজিক বনায়নে সাধারণত আকাশমণি ও ইউক্যালিপ্টাস লাগানো হয়। দু’টি গাছেরই উৎস অস্ট্রেলিয়া। দীর্ঘদিন আগে আমাদের দেশে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় বা গল্পে শিলং পাহাড়ের কথা যেমন লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন সেই পাহাড়ি চায়ের বাগানে ইউক্যালিপ্টাস সারির কথা। এই দুই জাতের গাছ চা-বাগান হয়েই আমাদের দেশে এসেছে। প্রথমে ইউক্যালিপ্টাস, পরে আকাশমণি।
অস্ট্রেলিয়ার এই দুই জাতের দ্রুত বর্ধনশীল গাছ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে গেছে। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বের ৭৪টি দেশের মোট এলাকার ১৫ শতাংশ জুড়ে রয়েছে ইউক্যালিপ্টাস। দক্ষিণ আমেরিকার ৪৪ শতাংশ জমিতে, ব্রাজিলে ৫২ শতাংশ, ভারতে ২৫ শতাংশ এবং আফ্রিকার ৩৮ শতাংশ জমি-জুড়ে রয়েছে ইউক্যালিপ্টাস।
ইউক্যালিপ্টাস নিয়ে বিতর্ক শুরু, গত শতকের আশির দশকে। বিতর্কের সূত্রপাত ভারত থেকে। তখন গাছটির এতো বেশি প্রসার হচ্ছিলো যে, তা থামাতে বিতর্কের বিকল্প ছিলো না। ভারতের গুজরাটে বেশিরভাগ জমির মালিক দরিদ্র মানুষের কাছে জমি বর্গা দিয়ে টাকা পেতো। কিন্তু দরিদ্ররা বর্গার টাকা বা ফসল ঠিকমতো দিতে না পারায় এক সময় জমিতে ইউক্যালিপ্টাস লাগিয়ে মোটা অংকের টাকা আয়ের প্রচলন হয়। কমতে শুরু করে সেখানকার কৃষি উৎপাদন। জমির মালিকরা ইউক্যালিপ্টাস লাগিয়ে মাত্র ৫-১০ বছরে কয়েকগুণ টাকা পেতে শুরু করে। এছাড়া ইউক্যালিপ্টাসে-এর মণ্ড থেকে উন্নতমানের কাগজ তৈরি হয়। ফলে মণ্ড আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করতে থাকে ভারত। এতে দরিদ্র মানুষের বিপদ বাড়ে। সোচ্চার হয়ে ওঠে মিডিয়া।

ইউক্যালিপ্টাস-এর বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখি হলো। ভারত এসব কথায় কর্ণপাত না করে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার মাধ্যমে কোন্ প্রজাতির গাছ কোন্ আবহাওয়ায় লাগানো যাবে, তা নির্ধারণ করে ইউক্যালিপ্টাস লাগাতে থাকে। গবেষণার মাধ্যমে নিজেদের আবহাওয়া উপযোগী নতুন নতুন জাতও উদ্ভাবন করে ভারত।
বলতে দ্বিধা নেই, একদিকে মিডিয়া এবং পরিবেশবাদীদের হৈ চৈ, অন্যদিকে গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত ভারত সরকারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। গবেষকরা সতর্ক করেন, ৪০০ মিলিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হয় এমন এলাকায় যেন ইউক্যালিপ্টাস না লাগানো হয়। এতে মাটির উর্বরতা নষ্ট হতে পারে। গবেষণা বলছে, ইউক্যালিপ্টাসের প্রায় ৮০০ জাত রয়েছে। কিন্তু সব জাত সব জায়গায় ভালো হয় না। ভারতে মাত্র ৫-৬ প্রজাতির ইউক্যালিপ্টাস লাগানো হয়।
ইউক্যালিপ্টাস নিয়ে প্রায় সবার অভিযোগ, এটি মাটি থেকে বেশি পানি শোষণ করে। ফলে মাটি শুকিয়ে যায়। যেখানে ইউক্যালিপ্টাস লাগানো হয়, সেখানে অন্য কোনো গাছ বা ফসল হয় না। বিশ্বব্যাপী এই বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণায় দেখা গেছে, ইউক্যালিপ্টাস মাটি থেকে যে পরিমাণ পানি গ্রহণ করে এবং তা থেকে যেটুকু কাঠ উৎপাদন হয়, অন্য প্রজাতির বৃক্ষ একই বা বেশি পরিমাণ পানি গ্রহণ করেও সেটুকু কাঠ উৎপাদন করতে পারে না। দেশীয় অনেক গাছ, যেমন সাদা কড়ই, ইউক্যালিপ্টাস-এর তুলনায় মাটি থেকে বেশি পানি শুষে নেয়, এমন প্রমাণও রয়েছে।
অনেকে বলেন, আকাশমণি’র ফুলের রেণু মানুষের শরীরে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে। এটি নাকি শ্বাসকষ্টেরও কারণ। প্রকৃত সত্য হলো, আকাশমণি’র ফুলের রেণুতে এক ধরনের আঠালো পদার্থ থাকে; যা বাতাসে ভেসে বেড়ায় না। শুধু পোকামাকড়ের মাধ্যমেই এর পরাগায়ন ঘটে।
ভারত যেমন গবেষণার মাধ্যমে কোন্ জাতটি কোন্ স্থানে লাগানো উচিত তা নির্ধারণ করেছে; বাংলাদেশেও ইউক্যালিপ্টাস নিয়ে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট বিস্তারিত গবেষণা করেছে। সত্যি বলতে কী, বাংলাদেশে ইউক্যালিপ্টাস-আকাশমণি নিয়ে যতো গবেষণা হয়েছে, দেশীয় কোনো প্রজাতি নিয়ে এতোটা হয়নি। এর প্রধান কারণ, বিদেশি গাছ দেশে জন্মানোর আগে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা হলে যে কোনো সময় বড় বিপদ ঘটতে পারে। যেমন- ২০০০ সাল পর্যন্ত শিশু আমাদের দেশে অর্থকরী গাছ হিসেবে পরিচিত ছিলো। কিন্তু মড়কের কারণে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে শিশু প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আবার কোনো দেশের দ্রুত বর্ধনশীল অনেক গাছ অন্য দেশে আগাছার মতো হয়ে যাতে পারে। যেমন- Prosopisjuliflora, মধ্য আমেরিকার দ্রুত বর্ধনশীল এই গাছ পাকিস্তান ও ভারতে আগাছায় পরিণত হয়েছে। এর শিকড় এতো গভীরে চলে যায় যে, কেটেও নির্মূল করা যায় না। তাই বিদেশ থেকে কোনো গাছ আনার আগে সঠিক গবেষণা ও সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে হয়। বলা প্রয়োজন, এসব মেনেই দেশে ইউক্যালিপ্টাস ও আকাশমণি’র প্রাতিষ্ঠানিক আগমন ঘটেছে।
বাংলাদেশে ইউক্যালিপ্টাস এবং আকাশমণি’র পূর্ণাঙ্গ গবেষণা শুরু হয় ষাটের দশকে। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ৪৯ প্রজাতির বীজ আমদানি করে। ১০ বছর গবেষণার পর দেখা যায়, মাত্র তিন প্রজাতির ইউক্যালিপ্টাস দেশে ভালো জন্মাচ্ছে। এই তিন প্রজাতি হলো- Eucalyptus camaldulensis, E. brassiana and E. terreticornis. এছাড়া চা বাগানে এবং বিভিন্ন জায়গায় শোভাবর্ধনকারী গাছ হিসেবে দেখা যায় আরও দুই প্রজাতির (E. citriodora and E. urophyla) গাছ। প্রাথমিক বাছাইপর্বে তেমন সাফল্য না পাওয়ায় এই দু’টি জাত পরে গবেষণায় রাখা হয়নি। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রথমোক্ত তিন জাতের বীজ সংগ্রহ করে নিবিড়ভাবে প্রভিন্যান্স ট্রায়াল করা হয়। এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়, কোন্ স্থানের বীজ দেশের কোন্ মাটি ও জলবায়ু উপযোগী। গবেষণায় দেখা গেছে, তিন প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে ভালো জন্মাচ্ছে পেটফোর্ড প্রভিন্যান্স। তৃতীয় পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এটি লাগিয়ে দেখা গেছে, সব ধরনের কৃষি পরিবেশ অঞ্চলেও জাতটি ভালো হচ্ছে। এরপর দেখা হয়, দেশের বিভিন্ন এলাকায় এর কাঠ উৎপাদন ক্ষমতা, রোগ-বালাই আক্রমণের হার, পরিবেশের উপর প্রভাব, অন্য গাছের সংগে এর আচরণ, এই গাছের ফলে অন্যকিছু জন্মাতে অসুবিধা হয় কি না, ইত্যাদি। সব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ শেষে ৮০০ জাত থেকে এই তিন প্রজাতির প্রভিন্যান্স অবমুক্ত করা হয়।
একইভাবে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট আকাশমণি’র ৮ জাতের গাছ এনে উপযুক্ততা যাচাই করে। এতে টিকেছে দুই (Acacia auriculiformis and Acacia mangium) প্রজাতি। ম্যানজিয়াম গাছটির বৃদ্ধি ভালো হলেও ৫-৬ বছর পর কাণ্ডে ছত্রাক আক্রমণ করে (heart-rot disease) বিধায় এটি বাদ দেওয়া হয়। আকাশমণি’র একাধিক প্রভিন্যান্স দেশের বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলে ট্রায়াল করে দেখা হয়, কোন্ প্রভিন্যান্স কোন্ কৃষি অঞ্চলে কেমন কাঠ উৎপাদন করে। এছাড়া দেখা হয়, অন্য প্রজাতির সংগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে কি না। গবেষণালব্ধ সব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের পর আকাশমণি’র বিশেষ একটি প্রভিন্যান্স বাংলাদেশে লাগানোর সুপারিশ করা হয়।
আরণ্যক ফাউন্ডেশন ২০১৫ সালে ‘ইউক্যালিপ্টাস ডায়ালেমা’ শিরোনামের এক প্রকাশনায় এই গাছের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যসহ প্রকৃত সত্য তুলে ধরে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়, সব জায়গায় এসব গাছ লাগানো ঠিক নয়। মাটির আর্দ্রতা বেশি আছে এমন স্থানে এই গাছ ভালো জন্মায়। তবে প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে এটি লাগানো উচিত নয়। সবচেয়ে উত্তম হলো, একক বাগানের বদলে এই গাছের মিশ্র বাগান করা।
উল্লেখ্য, গবেষণার সাফল্য মাঠ পর্যায়ে নেওয়ার আগে কৃষি বনায়ন কর্মসূচির আওতায় দেশের উত্তরাঞ্চলে ফসলের সংগে ইউক্যালিপ্টাস, আকাশমণিসহ ৩৬ ধরনের গাছ লাগিয়ে কোন্ গাছের সংগে কোন্ ফসলের কেমন প্রতিক্রিয়া হয়, তা নির্ধারণ করা হয়। এতে দেখা যায়, আট মিটার দূরে দূরে ফসলের মাঠে ইউক্যালিপ্টাস বা আকাশমণি লাগালে ফসল ক্ষতির সর্বোচ্চ পরিমাণ মাত্র ১২%। কিন্তু গাছ থেকে যে অর্থ বা জ্বালানিকাঠ আসে, তাতে লাভ হয় ক্ষতির তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। চাষীদের সম্পৃক্ত করেই গবেষণাটি করা হয়। শুরুতে ফসলের ক্ষেতে গাছ লাগানোর পরীক্ষায় অংশগ্রহণে শঙ্কিত থাকলেও, গবেষণার ফলাফল দেখে তাঁরা গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।
বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলে পতিত-জমি থেকে শুরু করে সর্বত্র আকাশমণি ও ইউক্যালিপ্টাস প্রসারের প্রধান কারণ হচ্ছে, গবেষণার সুফল। যদিও অনেকে বলেন, আকাশমণি’র ফুলের রেণু মানুষের শরীরে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে। এটি নাকি শ্বাসকষ্টেরও কারণ। প্রকৃত সত্য হলো, আকাশমণি’র ফুলের রেণুতে এক ধরনের আঠালো পদার্থ থাকে; যা বাতাসে ভেসে বেড়ায় না। শুধু পোকামাকড়ের মাধ্যমেই এর পরাগায়ন ঘটে।
ইউক্যালিপ্টাস এবং আকাশমণি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এক পর্যায়ে সরকারি অর্থে সরকারি জমিতে ইউক্যালিপ্টাস লাগানো বন্ধের আদেশ জারি হয়। এই সময় সংশ্লিষ্ট গবেষক ও উন্নয়ন-কর্মীদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বেশক’টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি আয়োজন করা হয় ১৯৯৬ সালে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে। সর্বশেষ ২০১৬ সালে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট জাতীয় পর্যায়ের এক কর্মশালায় ইউক্যালিপ্টাস ও আকাশমণি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। এসব কর্মশালার সুপারিশ হচ্ছে, গাছ দু’টি নিয়ে যেসব অভিযোগ তোলা হয়, তা পুরোপুরি সত্য নয়।
আরণ্যক ফাউন্ডেশন ২০১৫ সালে ‘ইউক্যালিপ্টাস ডায়ালেমা’ শিরোনামের এক প্রকাশনায় এই গাছের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যসহ প্রকৃত সত্য তুলে ধরে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়, সব জায়গায় এসব গাছ লাগানো ঠিক নয়। মাটির আর্দ্রতা বেশি আছে এমন স্থানে এই গাছ ভালো জন্মায়। তবে প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে এটি লাগানো উচিত নয়। সবচেয়ে উত্তম হলো, একক বাগানের বদলে এই গাছের মিশ্র বাগান করা।
কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা
আমরা অনেক সময় সঠিক তথ্য না জেনেই কল্পনাপ্রসূত বক্তব্য দিই; যা মোটেই সমীচীন নয়।
একদা এক বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলভিকালচার পড়াতাম। ক্লাসে গিয়ে দেখি, ছাত্র-ছাত্রীরা ইউক্যালিপ্টাসকে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ গাছ হিসেবে জানে। কারণ জানতে চাইলে জানালো, অমুক স্যার বলেছেন। আমি তাদের স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বললাম, আল্লাহ’র কোনো সৃষ্টি খারাপ হতে পারে না। সাপ, বাঘ বা সিংহকে আমরা ভয়ঙ্কর প্রাণী হিসেবে জানি। কিন্তু তাদের উপস্থিতি কতো প্রয়োজন, তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? বাঘ না থাকলে হরিণের সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো? সুন্দরবনের কী অবস্থা হতো? ইঁদুর প্রতিবছর শত শত কোটি টাকার ফসল নষ্ট করে। তবু সাপ না থাকলে ইঁদুরের উৎপাত কি সহনীয় থাকতো? মাছ এবং প্রাণিসম্পদ বিষয়েও তাদের ধারণা দিতে চেষ্টা করি। দেশের মানুষের প্রোটিন চাহিদা মেটাতে আমরা ব্রয়লার বা লেয়ার এনেছি। পাঙ্গাস, তেলাপিয়াসহ নানান জাতের কার্প এনেছি। কতো ফলের গাছ এনেছি বিদেশ থেকে। শুধু দেশীয় মাছ বা মুরগি দিয়ে কি আমাদের চাহিদা মেটাতে পারতাম? তাই একতরফা বিদেশি প্রজাতিকে দূরে ঠেলে দিলে হবে না। আমাদের এবং বিশ^মানবের কল্যাণে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের দেশে যে জীববৈচিত্র্য আছে, তা ইউরোপ-আমেরিকায় নেই। তাই উন্নত জাতের দ্রুত বর্ধনশীল সব প্রজাতির পাশাপাশি দেশীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।
সিদ্ধান্ত নিলাম, ছাত্র-ছাত্রীদের বনে নিয়েই সিলভিকালচার পড়াবো। প্রথমে শালবনে (মৌচাক) নিয়ে গেলাম। সেখানেই বনবিভাগ প্রথম সামাজিক বনায়ন পদ্ধতিতে কৃষি-বনায়ন চালু করে; যার অংশীদার স্থানীয় দরিদ্র জনগণ। মৌচাকে একদিকে রয়েছে ইউক্যালিপ্টাস-আকাশমণি’র সংগে আনারস বা সবজি, অন্যদিকে প্রাকৃতিক শালবন।

ছাত্র-ছাত্রীদের বললাম, অংশীদারদের সংগে আলোচনা করে জেনে নাও, কেন তাঁরা আকাশমণি ও ইউক্যালিপ্টাস লাগিয়েছেন? এসব গাছ তাঁদের কী ক্ষতি করছে? শাল না লাগিয়ে তাঁরা কেন বিদেশি গাছ লাগালেন?
অংশীদারদের সংগে প্রায় ছয় ঘণ্টা আলোচনা করলো ছাত্র-ছাত্রীরা। এরপর প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে একটি করে খাতা দিলাম। লিখতে বললাম, তাদের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষণের কথা। সব শেষ প্রশ্ন ছিলো, দায়িত্ব পেলে তুমি এই বনের ব্যবস্থাপনা কী করতে?
মজার বিষয়, স্থানীয়দের সংগে আলাপ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মাথা গুলিয়ে যায়। যে দু’টি গাছকে তারা সবচেয়ে খারাপ বলে জানে, সেই দু’টিই অংশীদারদের পছন্দ। অংশীদাররা এ-ও জানালেন, দীর্ঘদিন ধরে শাল-এর কপিস কাটতে থাকায় সেখানে শাল-এর চারা নেই বলেই শাল লাগানো হয়নি। মাঝে মাঝে দুয়েকটি শাল দেখা গেলেও তা দুর্বল। শাল থেকে পাতা-কাঠ পেতে অপেক্ষা করতে হয় ৪০-৫০ বছর। ইউক্যালিপ্টাস বা আকাশমণি থেকে মাত্র দশ বছরে কাঠ পাওয়া যায়। এছাড়া, আকাশমণি বা ইউক্যালিপ্টাস-এর নিচে শাল-এর অনেক চারা দেখা যাচ্ছে। এই গাছগুলো কাটার পর এটি শালবনে পরিণত হবে।

আকাশমণি মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ায়, অংশীদারদের কাছে এমন তথ্য জেনে ছাত্ররা বিভ্রান্ত। কী লিখবে, ভেবে পায় না। এতোদিন জেনেছে, ইউক্যালিপ্টাস-এর নিচে কিছুই হয় না। অথচ মাঠে এসে দেখলো, শুধু ফসল নয়, শাল-এর চারাও রয়েছে। আকাশমণি’র নিচেও নানান জাতের চারা রয়েছে। এতোদিন যা জানতো, এর বিপরীত চিত্র দেখে তারা কী লিখবে? ইউক্যালিপ্টাস ও আকাশমণি, খারাপ না ভালো?
অংশীদারদের কথা এবং নিজেদের অভিমত মিলিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হলেও তারা একটি বিষয় সুস্পষ্ট বুঝতে পারলো, কোনো বন গাছশূন্য হলে কিংবা মাটির উর্বরতা কমে গেলে, সেখানে আকাশমণি লাগিয়ে মাটির উর্বরতা ফিরিয়ে আনা যায়। তারা লিখলো, বন ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পেলে প্রথম ১০ বছর ন্যাড়া এলাকায় আকাশমণি লাগাবে। মাটির স্বাস্থ্য ভালো হয়ে গেলে, শালবাগান এলাকায় এমনিতেই হাজার হাজার শাল-এর চারা জন্মাবে। এরপর দুর্বলগুলো কেটে এক গাছ থেকে আরেক গাছের নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বন-সৃজন করবে।
আমি ভাবনায় পড়লাম। তারা কি আমাকে খুশি করতে এমন লিখেছে? পরদিন ক্লাসে গিয়ে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম। স্যার, আমরা কি ভুল জানতাম? সত্যিই কি গাছগুলো ভালো? সত্যিই কি ইউক্যালিপ্টাস-এর কাঠ দিয়ে ফার্নিচার হয়? গাছটি কি মাটি থেকে বেশি পানি শুষে নেয় না? এর নিচে ফসল হয়? তাহলে এই গাছ সম্পর্কে এতো অপপ্রচার কেন?
আমরা যে দু’টি গাছকে খারাপ জানতাম, সাধারণ মানুষ মোটেও তা মনে করেন না। বরং এই গাছের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে। ভালো ফসল হয় না এমন জমিতে তাঁরা ইউক্যালিপ্টাস এবং আকাশমণি লাগাচ্ছেন।
আমি তাদের কিছু গবেষণা প্রবন্ধ পাঠ করতে বলি। আমার সিলভিকালচার পড়ানোটা ইউক্যালিপ্টাস এবং আকাশমণি বিতর্কেই যেন সীমিত হয়ে গেলো। পরীক্ষা শেষ। এবার ইন্টার্নশিপের পালা। কয়েকজন ছাত্র আমার সংগে ইন্টার্ন করতো চাইলো। আমি দু’জনকে নিলাম। ইউক্যালিপ্টাস এবং আকাশমণি নিয়ে কাজ করতে দিলাম। বললাম, তোমাদের কাজ হবে কমপক্ষে দুই সপ্তাহ সিরাজগঞ্জ ও বগুড়ায় গিয়ে বসতবাড়ি, নার্সারি, পতিত-জমি, ফসলের ক্ষেত ও আইল, স’মিল, ফার্নিচার দোকানসহ সম্ভাব্য সব স্থান পর্যবেক্ষণ করা। লোকজনের সংগে কথা বলে জানতে চেষ্টা করো, তাঁরা বিভিন্ন ধরনের গাছ কেন লাগাচ্ছেন? গাছগুলো তাঁদের কী উপকার এবং ক্ষতি করছে? তাঁরা এই জমিতে আগে কী করতেন? বর্তমানে কেমন ফসল উৎপাদন হচ্ছে? এসব গাছ বেশি পানি শুষে নেয় কি না? জমিতে গাছ লাগানোয় ফসল উৎপাদন কমেছে কি না? নার্সারিতে কী কী চারা উৎপাদন হয়? সেখানে ইউক্যালিপ্টাস ও আকাশমণি’র অংশ কেমন? চারা কোথায় বিক্রি হয়, দাম কতো? চারা বিক্রির হার কমছে না বাড়ছে? বীজ কোথায় পায়? চারা উত্তোলন পদ্ধতি কী? স’মিল থেকে জানতে চেষ্টা করো- কী কী কাঠ চিরাই হয়? এর মধ্যে ইউক্যালিপ্টাস ও আকাশমণি’র অংশ কতো? গাছের লগ কোত্থেকে আসে? কাঠ চিরাই করা কঠিন না সহজ? ফার্নিচারের দোকানে কী কী কাঠ ব্যবহার হয়? কোন্ কাঠ দিয়ে কী ফার্নিচার তৈরি হয়? দাম কেমন, চাহিদা কেমন ইত্যাদি।
আমার দুই ছাত্র ক্যামেরা, কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। দুই সপ্তাহ পর ফিরে এসে জানালো, আমরা যে দু’টি গাছকে খারাপ জানতাম, সাধারণ মানুষ মোটেও তা মনে করেন না। বরং এই গাছের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে। ভালো ফসল হয় না এমন জমিতে তাঁরা ইউক্যালিপ্টাস এবং আকাশমণি লাগাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, মাত্র ৫ বছরে গাছ থেকে যে টাকা আসে, ১০ বছর ফসল করেও তা মেলে না। জ্বালানি কাঠের চাহিদা মেটাতেও এই গাছের বিকল্প নেই। ১০ বছরের একটি গাছ ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করা যায়, অর্থাৎ বছরে হাজার টাকা। এক বিঘা জমিতে কমপক্ষে ৮০০ কাঠ-জাতীয় গাছ লাগানো যায়। কৃষি বনায়ন পদ্ধতিতে ফসলের সংগে আকাশমণি বা ইউক্যালিপ্টাস বিঘাপ্রতি গড়ে প্রায় ১০০ লাগানো যায়। অর্থাৎ ফসলের পাশাপাশি ১০ বছর পর গাছ বিক্রি করে বাড়তি এক লাখ টাকা। পতিত-জমিতে আকাশমণি বা ইউক্যালিপ্টাস বিঘাপ্রতি ৮০০ এবং হেক্টরপ্রতি ২৫০০ লাগানো যায়। ৮০০’র মধ্যে অর্ধেক গাছ ভালো না জন্মালেও ১০-১২ বছর পর প্রতি গাছে ১০,০০০ টাকা হিসাবে মোট আয় দাঁড়ায় চার লাখ টাকা। বস্তুত: মানুষ এখন সেই কাজই করছেন।
বাজারে আকাশমণি’র চাহিদা বেশি। এর কাঠ প্রায় সেগুন-কাঠের সমতুল্য। ইউক্যালিপ্টাস কাঠ বেশি শক্ত হওয়ায় চিরাইকালে ব্লেড বারবার ধার দিতে হয়। নার্সারিতে ইউক্যালিপ্টাস-এর লাল এবং সবুজ চারা পাওয়া যায়। লাল চারায় বৃদ্ধি কম হয়। তাই সবুজ চারার চাহিদা বেশি। নার্সারির ৯৫ শতাংশ চারা ইউক্যালিপ্টাস এবং আকাশমণি’র। ফলের মধ্যে আম, লিচুর কলম এবং মেহগনি ও ঘোড়ানিমের চারা উল্লেখযোগ্য। মড়কের ভয়ে এখন কেউ শিশু’র চারা কেনেন না। ফলে নার্সারিতেও কম পাওয়া যায়।

স’মিলের প্রায় ৬০ ভাগ কাঠ ইউক্যালিপ্টাস-এর এবং ৩০-৩৫ ভাগ আকাশমণি’র। অন্য কাঠের মধ্যে মেহগনি, রেন্ডিকড়ই দেখা যায়। বেশিরভাগ ফার্নিচার তৈরি হচ্ছে ইউক্যালিপ্টাস, আকাশমণি দিয়ে। অল্প কিছু মেহগনি’র।
নার্সারি মালিক এবং যারা বসতবাড়ি বা ফসলের জমিতে গাছ লাগিয়েছেন, তাঁদের দুয়েকজন ছাত্রদের বলেছেন, ইউক্যালিপ্টাস লাগানোয় জমির রস বা আর্দ্রতা কমেছে। তবে বেশিরভাগই বলেছেন, কোনো সমস্যা পাননি। যারা বলেছেন, জমির আর্দ্রতা কমেছে, তাঁদের সম্পূরক প্রশ্ন করা হয়- গাছটি কেটে ফেলেননি কেন? জবাবে বলেছেন, গাছ বড় হয়ে গেছে। কিছুদিন রাখলে মোটা অঙ্কের টাকা পাওয়া যাবে। আবার জানতে চাওয়া হয়, গাছ কাটার পর কি আবারও এই গাছ লাগাবেন? বেশিরভাগই জানিয়েছেন, লাগাবেন।

নার্সারি মালিকরা বলেছেন, আগে ভালো বীজ পাওয়া যেতো। দিনদিন বীজের মান খারাপ হচ্ছে। নার্সরিতে নানান চারা উৎপন্ন হয়। কোনোটি দ্রুত বাড়ে। কোনোটির রং ভিন্ন হয়। কোনোটি লাগালে গাছ ভালো হয় না। বীজের গুণগতমানে কম গুরুত্ব দেওয়ায় গাছের উৎপাদন কমছে বলে মনে করেন নার্সারি মালিকরা।
আরও পড়ুন: নন্দ ঘোষ-ইউক্যালিপ্টাস ও আমাদের দেখনদারি রক্ষণশীলতা
বাংলাদেশে গবেষণা পর্যায়ে ২০-৩০ ঘনমিটার কাঠ পাওয়ার কথা বলা হলেও আকাশমণি এবং ইউক্যালিপ্টাস বছরে হেক্টরপ্রতি গড়ে প্রায় ১০ ঘনমিটার কাঠ দেয়। ব্রাজিলে হেক্টরপ্রতি ৬০ ঘনমিটার। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সঠিক বীজ ব্যবহার করলে কমপক্ষে ১৫ ঘনমিটার কাঠ পাওয়া যেতো। পক্ষান্তরে দেশীয় গাছ হেক্টরপ্রতি গড়ে ২-২.৫ ঘনমিটার কাঠ দেয়। তাই কাঠের বাড়তি চাহিদা মেটাতে এসব গাছের বেশি বেশি চাষ প্রয়োজন। তবে গাছগুলো কোথায় লাগাতে হবে, এর একটি সীমারেখা টানা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনো প্রাকৃতিক বনে আকাশমণি লাগানো উচিত নয়। কারণ, এই গাছের বীজ মাটিতে পড়ে ঘন হয়ে চারা গজায়; যা বনের প্রতিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বসতবাড়িতে বা পতিত-জমিতে এই গাছ লাগানো যেতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো ঝোঁপ-ঝাড় কেটে আকাশমণি বা ইউক্যালিপ্টাস লাগানো উচিত নয়। এসব ঝোঁপ-ঝাড়ে থাকা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলও নষ্ট করা ঠিক নয়।
লিগিউম জাতীয় গাছ আকাশমণি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে মাটিকে উর্বর করে। এজন্যই চা-বাগানে এর কদর বেশি। দুর্বল মাটিতে এই গাছ লাগিয়ে উর্বরতা বাড়ানো সম্ভব। কপিসিং হওয়ায় কাটার পর গোড়া থেকেই আবার এই গাছ হয়। তবে ভালো বীজের উৎস তৈরি এবং নার্সারিতে ভালো বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। তবেই কৃষির অন্য সেক্টরের মতো বনও সমানতালে এগিয়ে যাবে।
লেখকঃ সাবেক নির্বাহী পরিচালক, আরণ্যক ফাউন্ডেশন।
[এই লেখা নিয়ে কারো ভিন্নমত থাকলে, লেখক তা জানতে আগ্রহী। বিভিনিউজ২৪-ও ভিন্নমতকে স্বাগত জানায়। তবে এই সংক্রান্ত ব্যাখ্যা বা আলোচনা অবশ্যই যৌক্তিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে।]
বিভি/এসডি




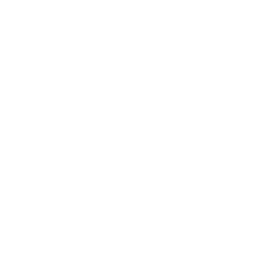
















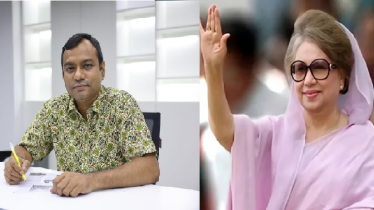
মন্তব্য করুন: